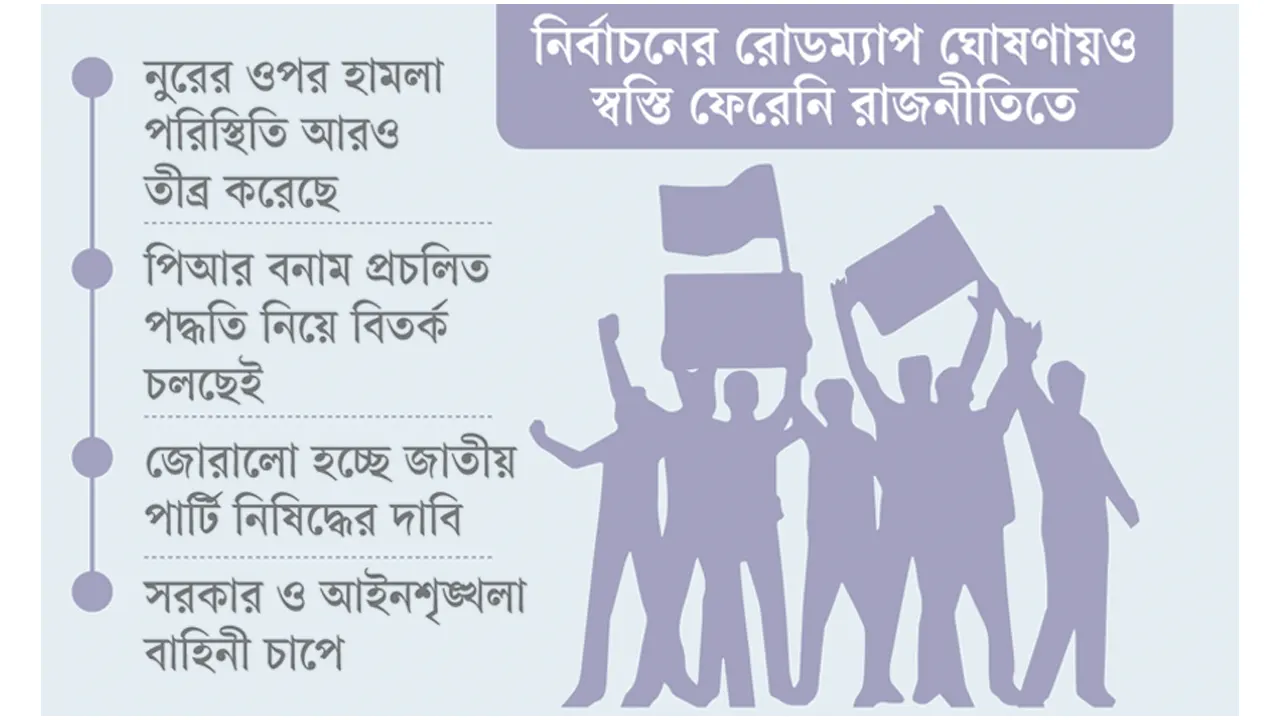পাহাড়ের বিদ্রোহ: ‘একমাত্র উপায়’ মিথের আড়ালে

জি. এম. আহমেদ : পাহাড়কে প্রথম দেখায় প্রশান্তির প্রতিচ্ছবি মনে হতে পারে; যেন অপার সৌন্দর্য আর অনাদি স্থিতির প্রতীক। তাই বলে পাহাড়ের শান্ত নীরবতা সবসময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশের ইঙ্গিত দেয় না। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এর জীবন্ত উদাহরণ। এখানে জমে আছে দীর্ঘ টানাপোড়েন আর অশান্তির ইতিহাস। এই ইতিহাস শুধু জমি বা রাজনীতির কাহিনি নয়- এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে ক্ষোভ ও হতাশার গল্প, অধিকার খোঁজার লড়াই, আর ভাঙা-গড়া স্বপ্নের নিত্য পথচলা।
এরই মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচিত অধ্যায় হল-পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) এবং এর সশস্ত্র সংগঠন শান্তি বাহিনীর বিদ্রোহ। তাদের দাবিÑশান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা বাধ্য হয়েছিল অস্ত্র ধরতে। সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাÑকর্মীর বাইরেও পাহাড় ও সমতলের আপামর জনগণের অনেকের কণ্ঠে এই দাবি প্রায়শই অনুরণিত হয়েছে।
কিন্তু প্রশ্ন হলো- এই দাবির রুঢ় সত্যতা কতটা? পাহাড়ের সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রকৃত শুরুটা কোথায়?
ইতিহাসের পাতায় তাকালেই বোঝা যায়- মূল গল্পটা অনেক বেশি জটিল।
সত্যিই কি সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল শেষ বিকল্প?
সন্ত লারমা, পিসিজেএসএসের বর্তমান সভাপতি ও শান্তি বাহিনীর প্রাক্তন ফিল্ড কম্যান্ডার একাধিকবার বলেছেন যে, শান্তিপূর্ন উপায়ে আন্দোলনের সব পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য, তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ৭ই জানুয়ারি ১৯৭৩ তারিখটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যেদিন তারা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়া, পিসিজেএসএসের ওয়েবসাইটে এখনও দাবি করা হচ্ছে যে, শান্তিপূর্ণ পথ শেষ হলে অস্ত্রই ছিল “একমাত্র উপায়” তাদের জনগণকে রক্ষা করার।
কিন্তু এই দাবির পেছনে কি সব কিছু সত্যিই সঙ্গতিপূর্ণ?
বাংলাদেশের এই পাহাড়ি অঞ্চলে কি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পথ সত্যিই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?
হয়তো না।
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তৎকালীন সরকারের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ ও খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতেন এবং তা করেছিলেনও। অন্যদিকে, এমনকি সশস্ত্র সংঘাত শুরু হওয়ার পরেও, কোনো সরকারই এই অঞ্চলে রাজনৈতিক কার্র্যক্রম নিষিদ্ধ করেনি।
এই প্রেক্ষাপটের সত্যতা নিশ্চিত করা যায় কেননা-পিসিজেএসএস নিজেই নিয়মিত এর সকল কার্যক্রম যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছিল।
আর কিছু না হলেও, এটুকু স্পষ্ট যে অন্তত ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়গুলো সংগঠনগুলোর জন্য পুরোপুরি অবারিত ছিলো। সেক্ষেত্রে, ‘শান্তি বাহিনী’ গঠন করা কি সত্যিই বিকল্প হিসেবে যুক্তিসঙ্গত ছিল?
এম.এন. লারমা, যিনি এই সশস্ত্র বিদ্রোহের মূল স্থপতি ছিলেন, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় বাকশালে যোগ দেন। তৎকালীন সরকারের রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তিনি পাহাড়ের গুমোট পরিবেশে শান্তির সুবাতাস বইবে বলে আশাবাদী ছিলেন- তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রকাশ্যে সরকারি দলে যোগ দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা প্রকাশ করার পাশাপাশি গোপনে সশস্ত্র কার্যক্রম চালানো নিঃসন্দেহে এক পরস্পরবিরোধী অবস্থান।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো- সশস্ত্র বিদ্রোহ ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। যা একদিকে অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা ও প্রস্তÍুতির ইঙ্গিত দেয় এবং অন্যদিকে ‘শেষ আশ্রয়’ বা ‘একমাত্র উপায়’ থেকে প্রত্যাশিত ধীর, ক্রমান্বয়ে শুরুর ধারণার বিরোধী।
অতএব, “গণতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক স্থান না থাকায় অস্ত্রধারণ” তত্ত্বটি বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না। সেক্ষেত্রে, প্রশ্নটা রয়েই যায়Ñ আসলে শান্তিপূর্ণ পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, নাকি অস্ত্রধারন ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত?
শেকড়ের গভীরেঃ কাপ্তাই বাঁধ ক্ষোভের শুরু:
পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহের শিকড় খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হবে পাকিস্তান আমলে, বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকে। তখন কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। কিন্ত এই বাঁধের ফলে পাহাড়ি-বাঙ্গালি মিলিয়ে প্রায় লাখখানেক মানুষ বাস্তচ্যুত; তলিয়ে যায় তাদের চাষাবাদের জমি ও বসতভিটা। যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সৃষ্টি হয়, হতাশা ও ক্ষোভ। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, সরকারের শিক্ষা বিস্তারমূলক পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং স্থানীয়দের মনে রাজনৈতিক সচেতনতার উম্মেষ ঘটে। কিন্ত প্রথাগত ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্বÑবিশেষ করে সবচেয়ে প্রভাবশালী চাকমা সার্কেল চীফÑজনগণের স্বার্থে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ নেননি, যার ফলে জনগণ তাদের উপর আস্থা হারাতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষিত যুবকরা উপলব্ধি করেনÑ নিজেদেও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কন্ঠ প্রয়োজন।
১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা গঠন করেন উপজাতীয় কল্যাণ পরিষদ। একই সময়ে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি। যদিও নাম শুনতে সামাজিক বা পেশাজীবি সংগঠনের মতো; এর সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ি মানুষের রাজনৈতিক অধিকার অর্জন। খুব শিগগিরই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন এক মাত্রা দেখা দেয়Ñসশস্ত্র পন্থা। কিছু নেতা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিকে সমর্থন করলেও, বামপন্থী ধারার প্রাভাবে অনেকে মনে করতেন, শুধু অস্ত্রের মাধ্যমে তাদের অধিকার রক্ষা সম্ভব।
মার্কসবাদী চিন্তা ও গোপন বিপ্লবী সংগঠনের উত্থান
প্রকাশ্য একটি সংগঠন হবে- সবার জন্য উন্মুক্ত। সমাজের সব সম্প্রদায়ের মানুষÑ যারা পাহাড়ি স্বার্থ নিয়ে সচেতন ও কাজ করতে আগ্রহী- তারা এতে যুক্ত হতে পারবেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এরা কোনো ভাবেই গোপন সংগঠনের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানবে না।
অন্যদিকে, আরেকটি গোপন সংগঠনে কেবল মার্কসবাদী তত্ত্বে দীক্ষিত কর্মীরা থাকবেন। এই সংগঠনের হাতে থাকবে মূল নেতৃত্ব। এটি আসলে হবে এক ধরনের ছায়াত্রন্ত্র, যার সুতো থাকবে গোপন নেতৃত্বের হাতে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেয় ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই মে। সেদিন রাঙ্গামাটিতে এক গোপন বৈঠকে গঠিত হয় ‘রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি’ (আরসিপি)। বৈঠকে ঠিক করা হয়, পাহাড়িদের সামাজিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সব সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করা হবে। এ নিয়ে সিদ্ধার্থ চাকমা বলেনÑ“যদিও দলের নামকরণ সেই মুহূর্তেই হয়নি তবুও বলা যেতে পারে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সেই গোপন সভার ফলশ্রুুতি।” (১৩৯২ বঙ্গাব্দ; পৃ.১০০)
আদর্শেও উত্তরাধিকার: গণ মুক্তি ফৌজ থেকে শান্তি বাহিনী
আরসিপি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই শান্তি বাহিনীর আদর্শিক ও সংগঠনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে প্রকাশিত প্রচারপত্র “রাঙ্গামাটির কমিউনিস্ট পার্টির লাল ঝান্ডা এগিয়ে চলেছে” স্পষ্টভাবে ঘোষনা করেছিল:
“স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক রাঙ্গামাটি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রাম চলবেই।”
পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোতে, এমনকি ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের আগে, সন্তু লারমা পাহাড়ি যুবকদের গোপনে আরসিপিতে নিয়োগ শুরু করেছিলেন। সত্তরের নির্বাচনের পরপরই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংগঠনিক কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় আরসিপির সশস্ত্র শাখাÑপিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) বা গণ মুক্তি ফৌজ। আফতাব আহমাদ (১৯৯৩) নিশ্চিত করেছেন, গণ মুক্তি ফৌজের ব্যানারে আরসিপি তার সশস্ত্র ক্যাডারদের সংগঠিত করেছিল। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগেই সশস্ত্র সংগ্রামের পথে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। বস্তত, ১৯৭২ সালে সক্রিয় এই ‘গণ মুক্তি ফৌজ’-ই সময়ের প্রবাহে ১৯৭৩ সালের পর থেকে ‘শান্তি বাহিনী’ নামে অধিক পরিচিতি লাভ করে।
অল্প কথায় বলতে গেলে, শান্তি বাহিনীর কার্যক্রম, আদর্শ ও নেতৃত্ব সরাসরি আরসিপি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। আরসিপি ছিল আদর্শিক ভিত্তি, গণ মুক্তি ফৌজ ছিল সশস্ত্র সূচনা, পিসিজেএসএস ছিল রাজনৈতিক প্রকাশ, আর সেই ধারাবাহিকতারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল ‘শান্তি বাহিনী’। অর্থাৎ, শান্তি বাহিনী কোনো আকস্মিক সংগঠন নয়; বরং আরসিপি থেকে পিসিজেএসএস হয়ে গণ মুক্তি ফৌজের মাধমে গড়ে ওঠা দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক-সামরিক ধারাবাহিকতার ফলাফল।
তবে প্রকাশ্যে শান্তির পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং আড়ালে সশস্ত্র কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকা রাজনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই পরস্পরবিরোধী। সুবীর ভৌমিক (১৯৯৬) এই অবস্থানকে ‘দ্বৈত নীতি ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যভাবে একে দ্বিমূখী কৌশল কিংবা নৈতিক দ্ব্যর্থতা বলেও অভিহিত করা যায়। অর্থ্যৎ, এটি শুধু একটি কৌশলগত পদক্ষেপ ছিল না, বরং এম. এন. লারমার প্রকাশ্য অঙ্গীকার ও গোপন কর্মযজ্ঞের মধ্যে নিহিত গভীর অসামঞ্জস্যের প্রতিফলন।
এই আখ্যান কেন আজও প্রচলিত
ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের আগে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পথ খোলা ছিল এবং পরেও তা ছিল। সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরও বাংলাদেশে সরকার পার্বত্য চ্ট্টগ্রামে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেনি। এমনকি পিসিজেএসএস নিজেও তাদের নিয়মিত রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পেরেছিল।
তাহলে আবারও প্রশ্ন আসে: শান্তিপূর্ণ পথ খোলা থাকল্ওে কেন অস্ত্র হাতে নেওয়া হলো?
এর উত্তর পাওয়া যায় আরসিপি’র বিপ্লবী পরিকল্পনায়। তাদের লক্ষ্য ছিল গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা এবং যুদ্ধের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা: প্রেরণ হিসেবে কাজ করেছিল মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওবাদ। আরসিপি গঠন থেকে শুরু করে শান্তি বাহিনীর উত্থান-সবই ছিল ধারাবাহিকভাবে সাজানো পদক্ষেপ। তাই অস্ত্র হাতে নেওয়া কোনো অনিবার্য পদক্ষেপ ছিল না; এটি একটি সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। শান্তির দুয়ার খোলা থাকলে ও তার অস্ত্র হাতে তুলে ইতিহাসে যুদ্ধের অধ্যায় লিখন-যেখানে একপক্ষের খলনায়ক, অন্যপক্ষের মহানায়ক।
এই অঞ্চলের সশস্ত্র তৎপরতায় বহ পাহাড়ি ও বাঙালি মানুষ প্রিয়জন, বাড়িঘর এবং শান্তি হারিয়েছেন। তাই সশস্ত্র বিদ্রোহের ইতিহাস কেবল ঘটনার তালিকা নয়; এটি মানষের যন্ত্রণার, সংগ্রামের এবং স্বপ্নের অমীমাংসিত গল্প। প্রতিটি হারানো জীবন, প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি, প্রতিটি লঙ্ঘিত অধিকারÑসবই কালের গর্ভে চিরস্থায়ী ক্ষত হয়ে আছে। এগুলো স্বরণ করিয়ে দেয় যে শান্তি ও সমাধানের পথ এখনও যেন অধরা। তবে তা অসাধ্য নয়Ñএগুলো অর্জন করতে হবে সততা, স্বচ্ছছতা এবং সত্যের সঙ্গে; মিথ্যা দাবি বা প্রোপাগান্ডার প্রলোভন এড়িয়ে। এই পথ খুঁজে বের করা হবে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের দায়িত্ব, যারা অতীত থেকে পাঠ নিয়ে ভবিষ্যতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে; গড়ে তুলবে সমৃদ্ধ সভ্যতা ও মানবিক জনপদ।
জি. এম. আহমেদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অনুরাগী ও গবেষক